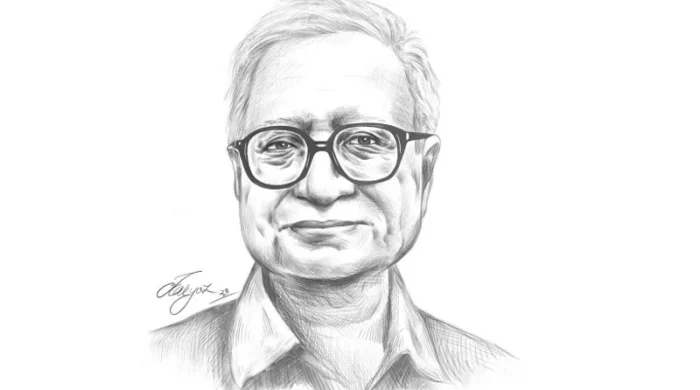
দেশে এক সময়ে বামপন্থি আন্দোলনের একটি শক্তিশালী ধারা প্রবহমান ছিল। বাম ধারায় কেবল সমাজতন্ত্রীরাই ছিলেন না। জাতীয়তাবাদীরাও দক্ষিণে নয়, বামেই ছিলেন। এখন দলীয় আনুগত্য নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদীরা সবাই দক্ষিণপন্থি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদবিরোধী বাম আন্দোলন এখন আর আগের মতো নেই। আন্দোলনকারী নেতারা অনেকেই হতাশার আক্রমণে ও প্রলোভনের বশে জাতীয়তাবাদী হয়ে গেছেন; কেউ কেউ রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে যে বামপন্থিরা এখনও টিকে আছেন তাদের ওপর নানাবিধ দমন-পীড়ন চলছে। জনমাধ্যমে প্রচারও তাদের জন্য প্রায়-নিষিদ্ধ। তরুণ তার বিক্ষোভ প্রকাশ করবে, এমন সংগঠন পায় না। সে যুক্ত হতে চায়; তার ভেতর আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্ষমতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা। তথাকথিত ইসলামপন্থি সংগঠনগুলোকে তারা অনেকটা হাতের কাছেই পেয়ে যায় এবং তাদের হাতছানিতে ধর্মীয় রাজনীতির পথে যাত্রা করে। বামের দৃশ্যমান অনুপস্থিতি যে জঙ্গি তৎপরতার একটি কারণ, সেটি বুদ্ধিমান উদারনৈতিক মানুষরাও বুঝতে চান না।
আর আছে মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাগত মান নিয়ে তো প্রশ্ন আছেই; সামগ্রিক বিচারে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা যে মঙ্গলজনক নয়, সেটি সব সময়েই অনুমানের ব্যাপার ছিল। এখন তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের মতো একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এই সংগঠনের ১৩ দফা দাবি অবিশ্বাস্য রকমের সরল, স্থূল এবং অন্ধকারমুখী। নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না; ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন করতে হবে– এমন বিপজ্জনক দাবিও রয়েছে।
হেফাজতে ইসলাম নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করে। কিন্তু তাদের প্রতিটি দাবি রাজনৈতিক এবং যে শক্তি তারা প্রদর্শন করেছে, সেটাকেও রাজনৈতিক ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ে চিহ্নিত করবার উপায় নেই। বুর্জোয়া দলগুলো তো বটেই, বর্তমান সরকারও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াত ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। ধনীরাই রাষ্ট্র চালান। তারা নিজেরা ইহজগৎ সম্পর্কে খুবই সচেতন। কীভাবে ধন বৃদ্ধি করা যায়, সে-চিন্তায় অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু সমাজে দার্শনিকভাবে ইহজাগতিকতার চর্চা হোক, এটা চান না। যারা ইহজাগতিকতার চর্চা করতে চান তাদেরকে শুধু সন্দেহ নয়, শত্রু বলেই বিবেচনা করেন। ফলে সমাজ এগোয় না। সমাজের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয় না। আমরা পশ্চাৎপদ রয়ে যাই। রাষ্ট্রের মালিকরা যা ইচ্ছা তাই করেন। সমাজ বদলের চেষ্টা গড়ে ওঠে না। আমাদের ভাবমূর্তি অপ্রতিরোধ্যরূপে মলিন হতে থাকে।
এমন অনেক শিক্ষিত লোকও আছেন, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শুনলে রীতিমতো শঙ্কিত বোধ করেন। ধারণা করেন, তাদের ধর্মচর্চার অধিকার নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে। যে জন্য রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করার সময় রাষ্ট্র পরিচালকদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবেই আশ্বাস দিতে হয়েছিল– ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। তার পরে রাষ্ট্র যখন পুরোপুরি পুরোনো সেই পুঁজিবাদী রাস্তায় চলা শুরু করল তখন তো আর কোনো রাখঢাক রইল না। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হলো। সরকারের বদল হয়েছে, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে পরিচিতরাও ক্ষমতায় এসেছেন। তাদের সময়ে নির্বাসিত ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরেছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বাহুল্য থেকে সংবিধানকে মুক্ত করার আগ্রহ দেখা যায়নি। পুঁজিবাদীরা খুবই বস্তুবাদী, কিন্তু ধর্মকে তারা নানাভাবে ব্যবহার করে থাকেন। বিভেদ সৃষ্টির জন্য, ভোটের জন্য, সর্বোপরি সামাজিক বিপ্লবে বিশ্বাসীদের দমন করার জন্য। বামপন্থিদের তারা সমাজদ্রোহী বলেও চিহ্নিত করেন। এমনও বলেন, ওরা হচ্ছে নাস্তিক।
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইহজাগতিকতা। রাষ্ট্র ও সমাজে এই দুটি গুণের কার্যকর উপস্থিতিই কি যথেষ্ট? না, তা নয়। গণতন্ত্রের জন্য তারা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এরা আছে বলেই রাষ্ট্র ও সমাজে যে গণতন্ত্র রয়েছে, তা অবশ্যই বলা যাবে না। এরা না থাকলে গণতন্ত্রের পথে এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য আরও কিছু দরকার। সেটি হলো সাম্য। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইহজাগতিকতা মানুষের জন্য মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে। ওই পথেই আবার পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে। সামন্তবাদের তুলনায় পুঁজিবাদ অগ্রসর বটে, কিন্তু পুঁজিবাদও বৈষম্যের ওপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদ গণতন্ত্র আনে না, গণতন্ত্রের জন্য প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ ‘কল্যাণ রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং নাগরিকদের ভোটাধিকার দেয়। কিন্তু গণতন্ত্রের যেটি মর্মবস্তু– অধিকার ও সুযোগের সাম্য সেটিকে নিশ্চিত করবে কি, উল্টো তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাই প্রয়োজন হয় পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের। ওই আন্দোলন না থাকলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইহজাগতিকতা উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়ে
পড়ে, যেমনটি আমাদের দেশে হচ্ছে; হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশেই।
পুঁজিবাদের সমালোচনা উদারনীতিকরা করে থাকেন। কিন্তু শেষ বিচারে তারা পুঁজিবাদের ধ্বংস চান না। চান সংস্কারের মধ্য দিয়েই তার সংরক্ষণ। সেদিক থেকে তারা আসলে রক্ষণশীলই। তারা ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত; পুরোপুরি দক্ষিণপন্থি হতে চান না, কিন্তু পুঁজিবাদের চাইতেও বড় বিভীষিকা মনে করেন সমাজতন্ত্রকে। সমাজতন্ত্রও এক ধরনের সামাজিকতাই; বৈষম্যহীন ও ইহজাগতিক সামাজিকতা। অর্থাৎ কিনা তার ধরনটি হলো উন্নত। সামাজিকতা না থাকলে মানুষ যে মানুষ থাকে না– সেটি তো স্বীকৃত সত্য। পুঁজিবাদ সামাজিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার কাজ মানুষকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক করা। যে জন্য পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে মানুষের প্রবণতা থাকে স্বার্থপর ও আত্মসুখপরায়ণ হওয়ার। আমরা যে গণতন্ত্র চাই, তার কারণ আমরা সামাজিকভাবে বাঁচতে চাই।
গণতন্ত্রের সংগ্রামে ধার্মিক লোকরাও থাকতে পারেন, থাকেনও। কিন্তু ধর্ম ব্যবসায়ীরা কখনোই থাকবে না। লাতিন আমেরিকার ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের একাংশকে দেখা গেছে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে। সম্প্রতি প্রয়াত বিশ্বক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি লাতিন আমেরিকার মানুষ। তাই দেখা যায়, অন্য কোনো পোপ যা কখনও করতেন না, তিনি তা করেছেন; পীড়িত বিশ্বের কথা বলেছেন। যেমন বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের শ্রমদাসত্বের ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
পুঁজিবাদবিরোধী মানুষ সমাজে আছেন। কিন্তু তারা
যে একত্র হয়ে মুক্তির অনুকূলে বড় একটি আন্দোলন গড়ে তুলবেন, তেমনটি ঘটেনি। আর ঘটেনি বলেই আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হয়নি; সমাজ পারেনি ইহজাগতিক হতে। আমরা পিছিয়ে আছি। এই সত্যটিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের একেবারে সামনে রাখা খুবই জরুরি।